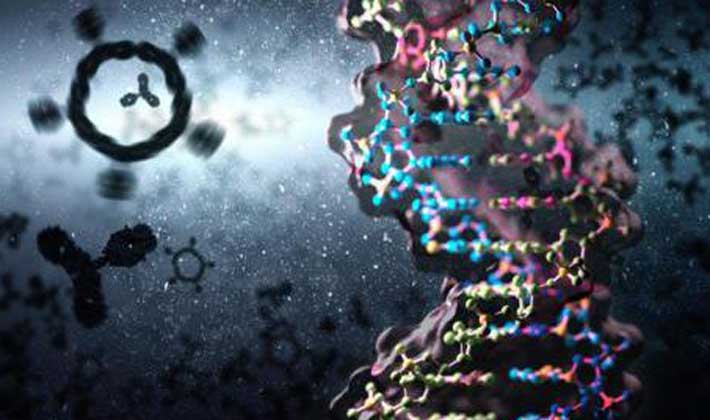
প্রাচ্য তাহেরের প্রবন্ধ ‘প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশ’
প্রকাশিত : সেপ্টেম্বর ১২, ২০২০
প্রাণ সৃষ্টির উৎস খোঁজার আগে পদার্থ বিষয়ে কিছু ধারণা নেয়া প্রয়োজন। যেসব উপাদান দিয়ে পদার্থ গঠিত, তাদের ভিত্তিতে পদার্থ তিন প্রকার। মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র। যেসব পদার্থের সমন্বয়ে উদ্ভিদ ও জীবদেহ গঠিত হয় তাকে বলে জৈব পদার্থ এবং বাদবাকিগুলো অজৈব পদার্থ। জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো, জৈব পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর কেন্দ্রে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু থাকে, যাকে কার্বন বলা হয়। কার্বনের বাংলা অঙ্গার বা ছাই। জৈব পদার্থ পুড়ালে সবসময় এই অঙ্গার পাওয়া যাবে। তাহলে বুঝা গেল, কার্বনই জৈব পদার্থের মূল উপাদান। কিন্তু এটিই শেষ কথা নয়। পদার্থবিশেষে এর সাথে মিশে থাকে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, গন্ধক এবং আরও অনেক পদার্থ। জৈব পদার্থের অণুর গর্ভস্থ কার্বনের সাথে এইসব পদার্থের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মিলনের ফলে জন্ম হয় ভিন্ন ভিন্ন জৈব পদার্থ। যেমন: কার্বন ও হাইড্রোজেন মিশালে পাওয়া যায় হাইড্রোকার্বন।
জীবদেহ যেহেতু জৈব পদার্থ, এর ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্যের। খাদ্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কার্বন সংগ্রহ করা। জীবজন্তু কার্বন সংগ্রহ করে লতাপাতা, তরিতরকারি, কীটপতঙ্গ, মাছ-মাংস ইত্যাদি থেকে। সংগৃহীত কার্বন বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে রূপান্তরিত হয় জৈব পদার্থে। উদ্ভিদ কার্বন সংগ্রহ করে বাতাস থেকে। কথা হচ্ছে, এই জৈব পদার্থ সৃষ্টি হলো কিভাবে? আকাশে আমরা যেসব নক্ষত্র দেখি তাদের মধ্যে আয়তন ও উত্তাপের পার্থক্য আছে। সর্বনিম্ন ৪০০০˚ সে. থেকে সর্বোচ্চ ২৮০০০˚ সে. উত্তাপের নক্ষত্র আছে। স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, খুব বেশি উত্তপ্ত নক্ষত্রদের কার্বন পরমাণুরা একা একা ভেসে বেড়ায়। এরা অন্যকোনো পরমাণুর সাথে জোড় বাঁধে না। কিন্তু যেসব নক্ষত্রের উত্তাপ ১২০০০˚ সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সেখানে কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে মিলে সৃষ্টি করেছে হাইড্রোকার্বন। এই হাইড্রোকার্বন একটি জৈব পদার্থ। এখান থেকেই জৈব পদার্থ সৃষ্টির সূত্রপাত।
কিন্তু পৃথিবীতে কার্বন সৃষ্টি হলো কিভাবে? আমরা জানি, সূর্যের বাইরের উত্তাপ প্রায় ৬০০০˚ সে.। সূর্যের মধ্যে একাধিক মৌলিক পদার্থের মিলন ঘটতে দেখা গেছে। সেখানে কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেন, কার্বনের সঙ্গে কার্বনের মিলন ঘটছে। ফলে সেখানে একাধিক জৈব পদার্থের জন্ম হয়েছে। উল্কাপিণ্ডের দেহ পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, উল্কার দেহে কার্বন ও ধাতুর মিলনে জন্ম হয়েছে কার্বাইড। এটাও একটি জৈব পদার্থ।
সূর্য, নক্ষত্র ও উল্কার দেহে যে প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ জন্ম নিয়েছে, পৃথিবীতেও একইভাবে প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে বর্তমানে যে পরিবেশ বিরাজমান, আদিতে এরকম ছিল না। পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহগুলো সূর্যের খণ্ডিত টুকরো। জন্মলগ্নে এই গ্রহগুলো ছিল জলন্ত এবং তাপমাত্রা প্রায় সূর্যের সমান। তখন এগুলো গ্রহ ছিল না, ছিল নক্ষত্র বা সূর্য। কোটি কোটি বছর জ্বলার পর এগুলোর জ্বালানি নিঃশেষ হয়ে গেলে এগুলো গ্রহে পরিণত হয়। সূর্য থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যকে আকর্ষণ করে প্রদক্ষিণ করছে। উপগ্রহগুলো গ্রহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই এগুলো গ্রহকেই আকর্ষণ করে প্রদক্ষিণ করছে। যেমন: চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। এটি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি অংশ, তাই চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে ঘুরছে। আদি পৃথিবীর জলন্ত সময়কালেই পৃথিবীতে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হয়।
প্রোটিন তৈরি হয় হাজার হাজার কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সুবিন্যস্ত সংযোগে। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটিন তৈরি হওয়ার মতো অনুকূল পরিবেশ ছিল। লাখ লাখ বছর ধরে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে হাইড্রোকার্বনের নানা রূপান্তরে তৈরি হয়েছিল প্রোটিন। এই প্রোটিন হতে জন্ম নিয়েছিল জীবদেহের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম। প্রকৃতির একমাত্র কাজ পরিবর্তন করা। এই পরিবর্তনই মূলত বিবর্তন। যা আমাদের চোখের গোচরে ঘটছে কিন্তু আমরা সেভাবে চিন্তা করছি না। তবে পৃথিবীতে বিভিন্ন বস্তুর বিবর্তনের সময়-কাল এক নয়। এদের মধ্যে ব্যবধান অনেক দীর্ঘ। বিবর্তনের জন্য যা জরুরি তা হচ্ছে, উপযুক্ত পরিবেশ। আমরা জানি, পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে পানি জমে বরফে পরিণত হয়। বরফ পানির বিবর্তিত রূপ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রকৃতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুধকে দইতে পরিণত করতে পারে, কিন্তু রেডিয়ামকে শীশায় পরিণত করতে সময় লাগে লাখ লাখ বছর। একইভাবে কার্বন (জৈব পদার্থ) হতে একটি প্রোটোপ্লাজম সৃষ্টি করতে প্রকৃতির সময় লেগেছে প্রায় একশো কোটি বছর।
পদার্থ জৈব হলেই তা জীব, একথা বলা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ না পায়। কোনো পদার্থে দেহপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি এই লক্ষণ দুটি যদি প্রকাশ পায় তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ওই পদার্থটি সজীব। প্রোটোপ্লাজমের মুখ্য উপাদান প্রোটিন এবং এটা ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জৈব-অজৈব পদার্থ। এটা আদিম সমুদ্রের জলে গোলা দ্রব অবস্থায় ছিল। এটা সম্পূর্ণ জলে মেশে না, জলের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকে। যার ইংরেজি নাম কলয়ডাল সলিউশন। এ সলিউশন জৈব বা অজৈব উভয় পদার্থের হতে পারে। অজৈব পদার্থের সলিউশন দ্রবীভূত হয়ে জলের নিচে পড়ে থাকে। এখানে জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে একটি চরিত্রগত পার্থক্য প্রকট হয়ে উঠেছে। জৈব পদার্থের সলিউশন জলে ভেসে থাকার সক্ষমতা অর্জন করেছে, পক্ষান্তরে অজৈব পদার্থের সলিউশন জলে আত্মসমর্পণ করেছে। জৈব কলয়ডাল সলিউশনের মধ্যে এই স্বকীয়তা দেখা গেছে যে, সে জলের শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজি নয়।
কলয়ডাল সলিউশনের মধ্যে একটি বিশেষ গুণ দেখা যায়। এটি জলে ভাসমান অন্য জৈব-অজৈব পদার্থকে আত্মসাৎ করে নিজ দেহ পুষ্ট করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া লাখ লাখ বছর চলতে থাকলে কলয়ডাল জৈব পদার্থটি আয়তন ও ওজনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং একটা পর্যায়ে এসে ফেটে দুই টুকরা হয়ে যায়। এই দুই টুকরো আগের মতো আলাদা আলাদাভাবে পুষ্ট হতে থাকে এবং আরও একটা পর্যায়ে এসে ফেটে চার টুকরো হয়ে যায়। কালের পরিক্রমায় চার টুকরো ফেটে হয় আট টুকরো। আমরা জানি, জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট হলো, পুষ্টি ও বংশবিস্তার করা। এই বিশেষ ধরনের কলয়ডাল পদার্থটির নাম প্রোটোপ্লাজম বা সেল। বাংলায় জীবকোষ বলা হয়। আদিম সমুদ্রের জলে অতি সামান্য প্রোটোপ্লাজম বিন্দুকে আশ্রয় করেই প্রথম প্রাণের অভ্যুদয় এবং পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল জীবনের অভিযান।
বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন, ‘প্রাণ’ শক্তিটি কোন কোন পদার্থের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি অভিনব শক্তি। পৃথিবীর আদি অবস্থায় তাপ, আলো, বায়ুচাপ, জলবায়ুর উপাদান ইত্যাদির পরিমাণ প্রাণ সৃষ্টির অনুকূল ছিল বলে তখন প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতির সেই আদিম অবস্থা আর নেই, তাই এখন চলছে বীজোৎপন্ন প্রাণ প্রবাহ বা প্রাণ থেকে প্রাণ উদ্ভবের ধারা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছিলেন কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করা যায় কিনা? ১৮২৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেড্রিক ওহলার টেস্টটিউবে ইউরিয়া (জৈব পদার্থ) তৈরি করে প্রমাণ করেন, প্রকৃতির (ঈশ্বর) ন্যায় মানুষ জৈব পদার্থ তৈরি করতে পারে। এরপর ১৯৬৭-৬৮ সালের শীতকালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আর্থার কোর্ণবার্গ এবং তার সহকারীরা মিলে টেস্টটিউবে অজৈব পদার্থ C. H. O. N. ইত্যাদির সংমিশ্রণে জৈব ভাইরাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। ওই ভাইরাস প্রকৃতজাত (ঈশ্বরসৃষ্ট) ভাইরাসের মতো নড়াচড়া করে।
প্রাণের বিবর্তন কিভাবে হয়েছিল? প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষের দিক পর্যন্ত জীবকোষগুলোর ইন্দিয়, চেহারা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়নি। সর্বশরীর দিয়ে চুষে এরা আহার করে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার পেলে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। আঘাত পেলে সর্বশরীরে শিহরণ ওঠে। এতে দেখা যায়, এসব জীবকোষে জীবনের আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে বোধশক্তি। বর্তমানে খাল-বিলের নোংরা জলে তুলতুলে জেলির মতো শেওলা জাতীয় এক প্রকার জলীয় পদার্থ দেখা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এদের শরীরে দেখতে পাওয়া যায় অসংখ্য বিন্দু বিন্দু জীবকোষ। এদের বলা হয় অ্যামিবা। এরা এককোষ বিশিষ্ট জীবজগতের আদিম প্রাণী।
ঋতু পরিবর্তনে প্রকৃতির মধ্যে এক প্রকার পরিবর্তন আসে তা স্বাভাবিকভাবে উপলব্ধি করা যায়। তেমনি কালের পরিক্রমায় কোনো কোনো আদিম জীবকোষের স্বভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসে। এরা একা একা না থেকে মৌমাছির মতো জটলা বেঁধে থাকতে আরম্ভ করে। জটলার বাইরের কোষগুলো খাদ্য সংগ্রহ করলে, তা ভেতরের কোষগুলো চুষে নেয় এবং স্বস্থানে থেকে এদের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হতে থাকে। এর ফলে জটলাটির আকৃতি বৃদ্ধি পায়। জটলার ভিতরের কোষগুলোর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকলেও বাইরের দিকের কোষগুলোর অবস্থা হয়ে পড়ে ভিন্ন। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির জটলা তৈরি হয়ে সমুদ্রজলে বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে।
আজ থেকে একশো কোটি বছর আগে ভূপৃষ্টের কোথাও উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল না। সমুদ্রের জল কিছুটা গরম, লবণহীন এবং এতে মিশে আছে নানা প্রকার জৈব-অজৈব পদার্থ। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল অত্যাধিক। আকাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে পতিত না হওয়াতে আকাশ ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। এ অবস্থায় ভূপৃষ্টের কোথাও সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না। বাতাসে আছে স্বল্পমাত্রার অক্সিজেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অধিক। এ পরিবেশে সমুদ্রের জলে জীবাণুদের বংশবিস্তার চলছিল ধীরে ধীরে। কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল হলে এবং আকাশের সব জলীয় বাষ্প ঝরে পড়লে, ভূপৃষ্টে অবাধে নেমে আসে সূর্যালোক। এই সূর্যালোক পেয়ে সমুদ্রজলে জীবাণুদের মধ্যে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।
সমুদ্রজলে যেসব জীবাণু রোদ পোহাবার সুযোগ পেল, তারা এক আশ্চর্য সুবিধা পেয়ে গেল। তারা দেখল, রোদ পোহালে ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। এতে ওইসব জীবাণু একস্থানে স্থির থেকে রোদ পোহায়ে দেহ পুষ্ট ও বংশবৃদ্ধি করতে লাগল। এরকম সুবিধাভোগী জীবাণুরা কালক্রমে উদ্ভিদে পরিণত হলো। আর যেসব জীবাণুরা জলের গভীরে থাকার কারণে সূর্যালোকের স্পর্শ পেল না, তাদের খাবার সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি না করে উপায় থাকল না। এসব অসুবিধাভোগী জীবাণুরা হলো জীব বা জন্তু।
গাছের পাতায় সূর্যের আলো পড়লে এক প্রকার সবুজ রঙের প্রলেপ পড়ে। একে বলা হয় ক্লোরোফিল। পাতার গায়ে বাতাস লাগলে ক্লোরোফিল বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করে একে কার্বন ও অক্সিজেন এই দুইভাগে বিভক্ত করে। কার্বনকে গাছের দেহপুষ্টির জন্য রেখে অক্সিজেন বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি সমুদ্রজলে যেসব জীবাণুদের শরীরে সূর্যালোক পড়েছিল, তাদের দেহে জমেছিল ক্লোরোফিল। ফলে এর সাহায্যে জীবাণুরা খাদ্য সংগ্রহ করে অচল জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। এরাই জাতিতে উদ্ভিদে পরিণত হয়। সে সময়ে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা ছিল অত্যাধিক। ফলে এসব উদ্ভিদাণুরা সহজে অতি মাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য কার্বন পেয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। বিবর্তনের ধারা অনুসারে এরা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করে। বিবর্তনের প্রথম ধাপে দেখা যায় শেওলা জাতীয় নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ।
সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত জীবাণুরা অন্য উপায়ে কার্বন সংগ্রহের চেষ্টায় থাকল। তারা উদ্ভিদাণুর দেহে প্রচুর কার্বন মজুত পেয়ে এদের খাওয়া শুরু করল। হাতের নাগালের খাবার শেষ হয়ে আসলে খাবার সংগ্রহের তাগিদেই তারা চলাফেরায় অভ্যস্ত হলো। উদ্ভিদাণুদের খেয়ে খেয়ে জীবাণুদের রাক্ষুসেপনা বেড়ে গেল। এতে সবল জীবাণুরা দুর্বল জীবাণুদের খেতে আরম্ভ করল। ফলে আত্মরক্ষার্থে দুর্বল জীবাণুরা পালাতে লাগল এবং সবল জীবাণুরা তাদের আক্রমণ করার জন্য তাড়া করতে লাগল। এতে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে দ্রুত চলাচলের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল। এভাবে বিবর্তনের ধারা মতে তারা বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।



























